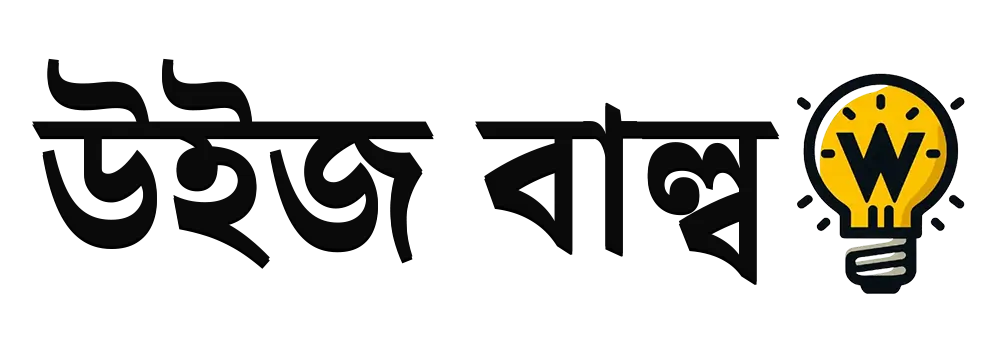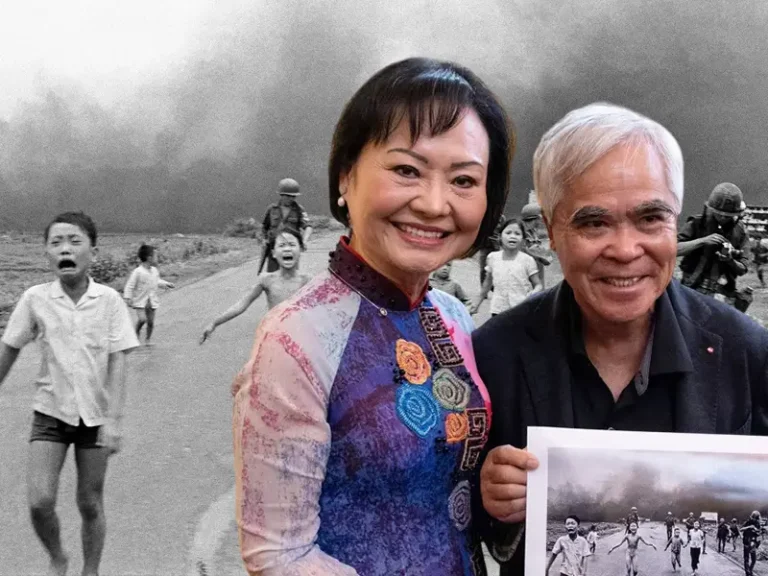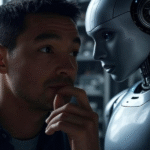ভ্যাম্পায়ার শব্দটি শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে কল্পনার এক রহস্যময় প্রাণী, যার অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে রক্তপান, রাত্রি, রসুন আর শবাধারে ঘুমানোর মতো বিষয়গুলো।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোককথা, উপন্যাস, চলচ্চিত্র আর টিভি সিরিজ মিলিয়ে এই চরিত্রের নানা রূপ তৈরি হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পরিচয় একটাই—তারা অন্ধকারের সন্তান, দিনের আলোয় অস্তিত্ব থাকে না তাদের।
তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে এই রূপকথাও। ভ্যাম্পায়ারের সম্পূর্ণ বিপরীত এক চরিত্র ‘ডেওয়াকার’ও এখন দেখা যায় বিভিন্ন কল্পকাহিনিতে। দিনের আলোয় ঘুরে বেড়ানো এসব ভ্যাম্পায়ারও ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে জনপ্রিয় ।
আসলে ভ্যাম্পায়ারের কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বিবর্তন হয়েছে। সূর্যের আলোতে এদের টিকতে পারা বা না পারার বিষয়টি কিন্তু সবসময় একই রকম ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিমের লোককাহিনী ভেদে এদের মধ্যে পার্থক্য ছিল।
যেমন – পূর্বে, মানে চীনে, যেসব ভ্যাম্পায়ার সদৃশ যেসব অস্তিত্ব ছিলো, তারা দিনের আলোতে দুর্বল হয়ে পড়তো ও ক্ষেত্রেবিশেষে ধ্বংস হয়ে যেতা। কিন্তু পশ্চিমের লোককাহিনীতে একটা লম্বা সময় পর্যন্ত এরা ধ্বংস হতো না। স্রেফ দিনে ঘুমাতো – এই যা।
তাহলে সূর্যের আলোতে বা দিনে এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো কীভাবে এলো? আর কীভাবেই বা সময়ের সাথে বদলেছে ভ্যাম্পায়ার চরিত্রের রূপ।
রাতের সন্তানদের উৎস
ভ্যাম্পায়ারের ধারণা অনেক পুরোনো। লোককথায় বরাবরই এই চরিত্র যুক্ত ছিল কবর, অন্ধকার আর রাত্রির সাথে। নানা সংস্কৃতিতে তাদের ঘিরে প্রচলিত ছিল বিচিত্র সব বিশ্বাস।
চীনের লোককাহিনীতে সরাসরি ভ্যাম্পায়ারের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও, এ ধরনের একটি চরিত্র ছিল – যাকে ডাকা হতো জিয়াংশি নামে।
এই জিয়াংশি আসলে জোম্বির মতো। চীনের বিভিন্ন লোককথা অনুসারে, জিয়াংশি হলো আদতে জীবন্ত লাশ। সেগুলোর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা হয় তাও জাদুর মাধ্যমে। এ ছাড়া কোনো আত্মা যদি দেহের ভেতরে আটকা পড়ে, সেক্ষেত্রেও এরকমটি হতে পারে। এগুলো ঠিক পশ্চিমের ভ্যাম্পায়ারের মতো রক্ত পান করে না। এরা মানুষের মধ্য থেকে জীবনীশক্তি শুষে নেয়।
এরা চলাচলও করে লাফিয়ে লাফিয়ে – দুই হাত সামনে তুলে, যেন কাউকে ধরতে আসছে। এগুলোর শরীর অসাড়। সেটিতে কোনো নড়াচড়া হয় না। বিভিন্ন লোককাহিনীর বর্ণনা অনুসারে, এই জিয়াংশি সূর্যের আলোতে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া তাদের আরেকটি দুর্বলতা হলো- ধান।
যেমন এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ভ্যাম্পায়াররা যদি কোনো বাড়ির সামনে ধান ছড়ানো অবস্থায় বা ধানের বস্তা দেখতে পায়, তাহলে তারা বাধ্য হয় প্রতিটি ধানের দানা গুণতে। এই কাজে তারা এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে সূর্য ওঠার খবরই পায় না। তখন দিনের আলোতে তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। এ কারণে বাড়ির সামনে ধান ছড়িয়ে রাখার এক কুসংস্কারও একসময় ছিল।
পশ্চিমের ভ্যাম্পায়ার
এদিকে, ইউরোপের সাহিত্যে প্রথম যে ভ্যাম্পায়ার চরিত্রগুলো এসেছিল— জন পলিডরি’র দ্য ভ্যাম্পায়ার (১৮১৯), জোসেফ শেরিডান লে ফানু’র কারমিল্লা (১৮৭২), কিংবা ব্রাম স্ট্রোকারের ড্রাকুলা (১৮৯৭)—সেই ভ্যাম্পায়াররা দিনের আলোয় কিছুটা দুর্বল হলেও একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যেত না।
নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজ অব টেকনোলজিতে গথিক সাহিত্য পড়ান অধ্যাপক লরা ওয়েস্টেনগার্ড। তিনি ভ্যাম্পায়ারদের সম্পর্কে জানান, তারা দিনে ঘুমাতে পছন্দ করত, কিন্তু আলোয় ভস্ম হয়ে যেত না।
তবে বড় পরিবর্তন আসে ১৯২২ সালে, এফ. ডব্লিউ. মুরনাউ পরিচালিত জার্মান সাইলেন্ট ফিল্ম নসফেরাতু-এর মাধ্যমে। স্ট্রোকারের ড্রাকুলা সিনেমার অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া এই সিনেমায় দেখা যায় কাউন্টি ওরলক নামের ভ্যাম্পায়ারটি সূর্যের আলোয় পড়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সহকারী অধ্যাপক স্ট্যানলি স্টেপানিক বলেন, “এই তিন সেকেন্ডের ছোট পরিবর্তনই একটা গোটা মিথকে বদলে দেয়। এরপর থেকেই সূর্যের আলো ভ্যাম্পায়ারদের জন্য মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে।”
ডেওয়াকারদের আবির্ভাব
১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে এসে ভ্যাম্পায়ারদের সূর্যালোক-সংবেদনশীলতা এতটাই প্রচলিত হয়ে যায় যে বিখ্যাত চশমা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রে ব্যান পর্যন্ত এক বিজ্ঞাপনে মজা করে দেখায়—ভ্যাম্পায়াররা তাদের সানগ্লাস পরে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই দিনের আলোতে ঘোরাঘুরি করতে পারছে!
অন্যদিকে, টোয়াইলাইট সিরিজের লেখিকা স্টেফানি মেয়ার দেখান, সূর্য ভ্যাম্পেয়ারের ত্বককে ঝলমলে করে তোলে, তাই তারা আড়াল খোঁজে।
তবে জনপ্রিয় কল্পকাহিনিতে পুনরাবৃত্তির ভেতর থেকেই জন্ম নেয় নতুন ভাবনা। এর অন্যতম উদাহরণ বলা যেতে পারে ব্লেডকে।
মার্ভেল কমিকে প্রথম ব্লেডের মূল চরিত্রটিকে দেখা যায় ১৯৭০-এর দশকে। সিনেমায় (১৯৯৮) তাকে দেখানো হয় এমন এক হান্টার হিসেবে, যার মা গর্ভাবস্থায় ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফলে ব্লেড (যার নামে গোটা কমিক সিরিজ) নিজে ভ্যাম্পায়ার হলেও তার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে দিনের আলোয় বেঁচে থাকতে পারে। এই কারণে তাকে বলা হয় ‘ডেওয়াকার’।
ব্লেডের এর এই দ্বৈত পরিচয়—ভ্যাম্পায়ার আর মানুষ দুইয়ের মিশ্রণে গড়া—তাকে আরো রহস্যময় ও শক্তিশালী করে তোলে। তাকে মুখোমুখি হতে হয় ভ্যাম্পায়ারদের দুটি গোষ্ঠীর সঙ্গে। এদের একটি হলো – ‘পিওরব্লাড’, যারা জন্মসূত্রে ভ্যাম্পায়ার, আর অন্যটি ‘মেইড’, যারা পরে কামড়ে ভ্যাম্পায়ার হয়েছে। রূপালী পর্দার সংস্করণে দর্শকরা দেখতে পান, ব্লেডের রক্ত ব্যবহার করে এক প্রাচীন দেবতাকে জাগানোর চেষ্টা করা হয় সিনেমার চূড়ান্ত মুহূর্তে।
আবার জনপ্রিয় বই ও টিভি সিরিজ ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিসে দেখা যায়, বিশেষ জাদুর আংটি ব্যবহার করে দিনের আলোতে ঘোরাফেরার সুযোগ পাচ্ছেন ভ্যাম্পায়াররা। তাদের মধ্যেও আবার ‘অরিজিনালস’ আছেন। তাদের আবার দিনের আলোতে ঘুরতে আংটি লাগে না, তারা এমনিতেই সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারেন। এরা মূলত প্রথম ভ্যাম্পায়ার, যাদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল ভ্যাম্পায়ারের যাত্রা। এদেরকেও তৈরি করা হয়েছিল জাদুর মাধ্যমে এবং এদেরকে ভ্যাম্পায়ার হয়ে উঠার জন্য যেতে হয়েছিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।
একটু খেয়াল করলে দেখবেন, এই যে ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিসের অরিজিনালস বা আসল ভ্যাম্পায়াররা – এদের সঙ্গে চীনের জিয়াংশির মিল রয়েছে। হয়তো এর লেখিকা এল.জে স্মিথ ও লিসা জে. স্মিথ সেসব লোককথা থেকেই নিজেদের ভ্যাম্পায়ারদের এসব বৈশিষ্ট্য ধার করেছেন।
মজার ব্যাপার হলো, এই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের এতো রূপ তৈরি হয়েছে, এটিই আসলে একে এতোদিন ধরে টিকিয়ে রেখেছে, যুগে যুগে মানুষের কাছে একে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। অধ্যাপক লরা ওয়েস্টেনগার্ড এ প্রসঙ্গে বলছেন, “ভ্যাম্পায়ারের কোনো একমাত্রিক রূপ নেই। বরং তার এই রূপান্তরশীলতাই তাকে করে তুলেছে চিরকালীন।”
অন্যদিকে অধ্যাপক স্টেপানিক বলছেন, “ভ্যাম্পায়ার এখন এমন এক প্রতীক হয়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে যেকোনো মানবিক অবস্থা বা অনুভূতির প্রতিফলন ঘটানো যায়।”
মোদ্দা কথা, ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে গল্প এখন আর শুধু আতঙ্ক বা রক্তপানের নয়—এটি হয়ে উঠেছে এক আয়না, যেখানে মানুষকে নিজেদেরকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। যান্ত্রিকতার এ যুগে বিষয়টি কী অদ্ভুত!
তথ্যসূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, পেনিব্লাড ডটকম
আপনার যদি এ লেখাটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে উইজ বাল্ব বুকমার্ক করে রাখুন। এরকম অভিনব ও নিত্যনতুন লেখা প্রায়ই পাবেন। আপাতত কষ্ট করে একটু ঢুঁ দিয়ে যেতে হবে সাইটে। চেষ্টা করছি নিউজলেটার অপশনও নিয়ে আসতে। সেটা চলে এলে সরাসরি আপনার মেইলেই চলে যাবে নতুন লেখা।