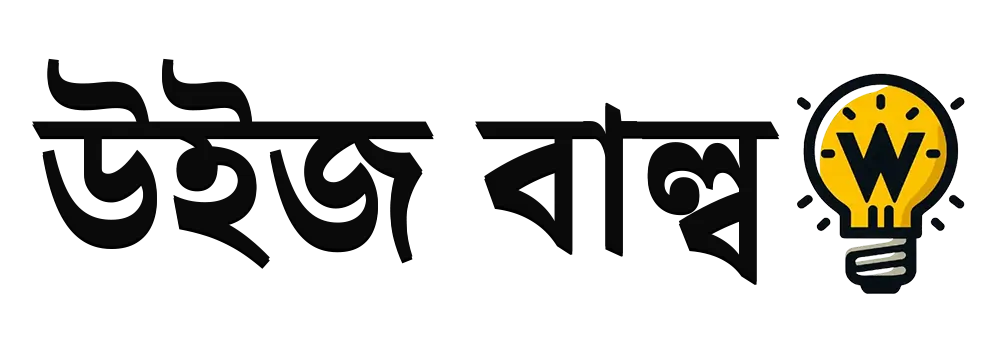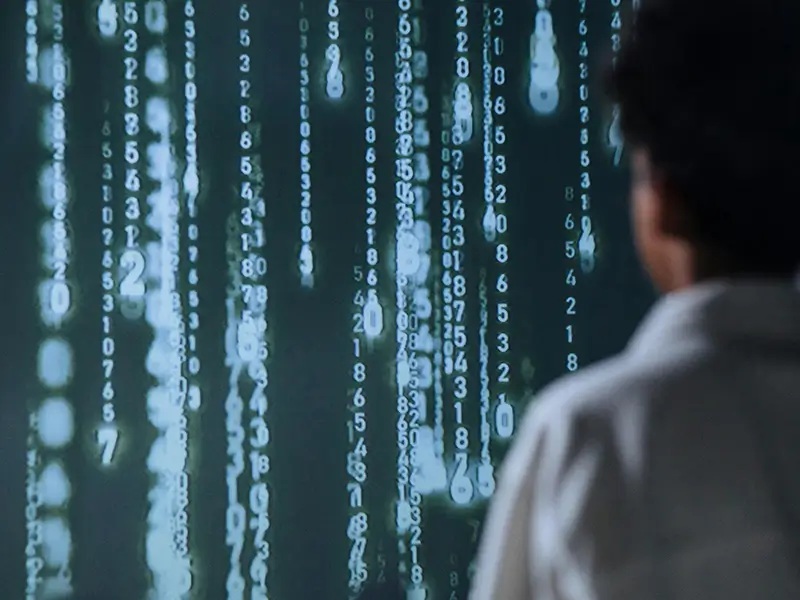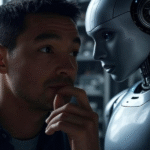২০২৫ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তির প্রভাবে প্রায় ৯০ লাখ চাকরি হারিয়ে যাবে। এটি মনগড়া কথা নয়। এই পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের Future of Jobs প্রতিবেদন।
একই সঙ্গে আশার কথাও আছে: ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। যার বেশিরভাগই হবে এমন, যেগুলোর অস্তিত্ব এর আগে কখনও ছিল না।
এই নতুন চাকরিগুলো কেমন হতে পারে তা বুঝার চেষ্টা করেছে খ্যাতনামা মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। চলুন প্রতিবেদনটির আলোকে দেখে নেওয়া যাক, ঠিক কী বলা হয়েছে।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন বলছে, এসব নতুন চাকরির বিষয়ে বুঝতে হলে আমাদের খুঁজে দেখতে হবে- ঠিক কোথায় ও কোন জায়গাগুলোতে মানুষের চাহিদা ও এআইয়ের দক্ষতার মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটানো সম্ভব? এআই কী করতে পারে, তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; ঠিক সেরকমই গুরুত্বপূর্ণ হলো – এআইয়ের কোন জায়গাগুলোতে মানুষকে প্রয়োজন?
মূলত তিনটা ক্ষেত্র আছে। যেখানে মানুষের চাহিদা সামনে বাড়বে, কোনো অংশেই কমবে না। না, এগুলো গতানুগতিক কোনো সেক্টর না।
এই তিন ক্ষেত্র হলো- বিশ্বাসযোগ্যতা (Trust), ইন্টিগ্রেশন (Integration) ও রুচি (Taste)। এগুলোতে মানুষ আগের চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।
বিশ্বাসযোগ্যতা: যন্ত্রের ভুল ধরার দায়িত্ব কার?
এআই আজ অবিশ্বাস্য দক্ষতায় লেখা, গণনা, এমনকি সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিতে পারে। কিন্তু যত বেশি মানুষ এআইয়ের ওপর নির্ভর করছে, ততই বড় একটি প্রশ্ন উঠে আসছে। আর তা হলো – এর ওপর আসলেও কতটা বিশ্বাস করা যায়?
এআই যে একেবারেই ভুল করে না, তা তো না। এআইয়ের হ্যালুসিনেট করা বা ভুল তথ্য দিয়ে দেওয়ার তথ্যটি সবারই কমবেশি জানা। এমনকি এআই চ্যাটবটের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত- ‘চ্যাটজিপিটি’র প্রতিষ্ঠাতা স্যাম অল্টম্যান পর্যন্ত বলছেন, এআইয়ের সব কথা বিশ্বাস না করতে।
তবে তা-ই বলে এআইয়ের ব্যবহার থেমে নেই। আর এ জায়গাতেই চলে আসছে মানুষের ভূমিকা। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির রবার্ট সিম্যান্স বলেন, ‘শিগগিরই সব বড় অ্যাকাউন্টিং ফার্মে “এআই অডিটর” থাকাটা নিয়ম হয়ে যাবে। এই পেশার মানুষদের কাজ হবে এআই কী করছে, কেন করছে—তা খুঁজে বের করে প্রযুক্তিগত, আইনি বা বাণিজ্যিক কারণে রিপোর্ট তৈরি করা।’
এর পাশাপাশি তিনি আরও একটি পেশার কথা ভাবছেন। সেটি হলো, এআই অনুবাদক বা Translator। এখানে এমন একজন ব্যক্তি কাজ করবেন, যিনি প্রযুক্তির গভীর বিষয়াদিগুলোকে ব্যবসার অন্যান্য স্তরে, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে সহজভাবে তুলে ধরতে পারবেন।
মোদ্দা কথা, তিনি হবেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি যন্ত্রের ভাষা মানুষকে ও মানুষের ভাষা যন্ত্রকে ঠিকঠাকভাবে বুঝিয়ে দিবেন। এই শূণ্যস্থান পূরণ করবেন।
এভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করতে গিয়ে সৃষ্টি হবে আরও অনেক নতুন পেশা। যেমন:
- ট্রাস্ট অথেন্টিকেটর বা ডিরেক্টর: এআই যে ডেটা বা সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, তা কতটা নির্ভরযোগ্য—তা যাচাই করার দায়িত্বে থাকবেন এরা।
- এআই এথিসিস্ট: নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরবেন। আদালত, বিনিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপকের সামনে এআইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে যৌক্তিক করে তুলবেন।
- আইনি গ্যারান্টর: এআই যদি কোনো চুক্তি তৈরি করে, তবে সেই চুক্তিতে শেষ পর্যন্ত সই করার জন্য মানুষেরই প্রয়োজন পড়বে। এমন একজন ব্যক্তিকে এখানে এগিয়ে আসতে হবে, যিনি সব বুঝে দায়ভার নিতে পারবেন।
- কনসিস্টেন্সি কো-অর্ডিনেটর: এআই এখনও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না। কোনো ডিজাইনের ২০টি সংস্করণ তৈরি করা হলেও, সেগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে মিলে না। এ ধরনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে লাগবে অভিজ্ঞ মানুষ।
- এস্কেলেশন অফিসার: গ্রাহকসেবায় যখন এআই ব্যর্থ হবে, তখন মানুষেরই তা সামাল দিতে হবে। কেউ একজন থাকবেন যিনি পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারেন।
স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এরিক ব্রিনজলফসন বলেন, “এআই যত জটিল হবে, দায়ভার নির্ধারণ ততই কঠিন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, কারও না কারও তো দায়িত্ব নিতে হবে।”
ইন্টিগ্রেশন: প্রযুক্তি জানলেই হবে না, বোঝাতে পারাও চাই
এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক কাজই হবে প্রযুক্তিনির্ভর। তবে শুধু কোড জানা বা মডেল বানানোই যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য চাই এআই ইন্টিগ্রেটর, যারা প্রযুক্তি ও ব্যবসা—দুই জগতকে বুঝতে পারেন।
সিম্যান্স বলেন, ‘সিইও বলবেন—আমরা এআইয়ে বিনিয়োগ করছি।’ কিন্তু কীসে? বিল পেমেন্ট? কর্মী নির্বাচন? নাকি ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন?” এই ‘কীসে বিনিয়োগ হবে’, তা খোঁজার কাজটা করবে ইন্টিগ্রেটর।
এদের কিছু সম্ভাব্য ভূমিকাগুলো হতে পারে:
- এআই প্লাম্বার: যন্ত্রাংশ ঠিক রাখার প্রযুক্তিবিদ নয়, বরং যখন এআই ‘অজানা’ সমস্যায় পড়ে—তখন সেটার উৎস খুঁজে বের করা ও ঠিক করার জন্য প্রয়োজন হবে এদের।
- এআই অ্যাসেসর: কোন মডেল কেমন পারফর্ম করছে, কীভাবে “হ্যালুসিনেট” করছে, কোনটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো, কোনটা অ্যালজেবরায়—এসব বিশ্লেষণ করা।
- এআই পারসোনালিটি ডিরেক্টর: এআইয়ের ব্যবহার মানুষের কাছে কেমন লাগবে? শীতল, বন্ধুসুলভ, বিদ্রুপাত্মক নাকি স্নিগ্ধ? সেটাই ঠিক করবেন এই ব্যক্তিরা।
- এআই ট্রেইনার: কোম্পানির ডেটা দিয়ে এআইকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিক ও ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়া তৈরি করার কাজ।
- এআই/হিউম্যান ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট: কোথায় শুধু এআই হলেই যথেষ্ট, কোথায় মানুষই ভালো, আর কোথায় দুজনের সমন্বয় প্রয়োজন—এই বিশ্লেষণ করবেন তারা।
রোবটিকসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেসব কারখানায় রোবট ব্যবহার হয়, সেখানে মানুষের চাকরি বাড়ে। কারণ সেই কারখানাগুলোর উৎপাদন বাড়তে থাকে, তারা ব্যবসা বেশি পায় এবং বাকি কারখানাগুলোকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু রোবট ইন্টিগ্রেটর না থাকলে রোবট স্থাপন করাই সম্ভব হয় না। এআইয়ের ক্ষেত্রেও তাই হবে। ইন্টিগ্রেটর থাকলে প্রতিষ্ঠান সামনে এগোবে, না থাকলে পিছিয়ে পড়বে।
রুচি: চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা এখনো মানুষের
রিক রুবিন-এর ভাইরাল “60 Minutes” সাক্ষাৎকারে সঞ্চালক জানতে চেয়েছিলেন, উনি কী কাজ করেন?
উত্তর ছিল: “আমি কোনো যন্ত্র বাজাতে পারি না, সাউন্ড বোর্ড চালাতেও জানি না… কিন্তু আমার রুচির ওপর আমার আত্মবিশ্বাস আছে।”
এআই দিয়ে লেখালেখি, ডিজাইন, মিউজিক—সবই এখন করা সম্ভব। কিন্তু কী লেখা হবে, কোন ডিজাইন হবে, কোন গান কাজ করবে—এই রুচির বিচার এখনও মানুষের।
ভবিষ্যতে লেখক নয়, একজন হতে পারেন আর্টিকেল ডিজাইনার। গল্প নয়, স্টোরি ডিজাইনার। এই রুচির প্রয়োগ একজন করতে পারেন হিউম্যান রিসোর্সেস ডিজাইনার হয়ে। প্রশিক্ষণ, সুবিধা, সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে একে কেন্দ্র করে।
গ্রাফিক ডিজাইনারকে হয়তো আর টাইপফেস নিজে বানাতে হবে না— এআই বানিয়ে দেবে। কিন্তু কোনটা বেছে নেবেন? কোথায় রাখবেন? কোনটা প্রভাব ফেলবে?—এটাই সত্যিকারের কাজ।
এই রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতার মূলে থাকবে।
যেমন, সব ফিন্যান্স কোম্পানি যদি সমান শক্তিশালী এআই ব্যবহার করে, তাহলে পার্থক্য কোথায় থাকবে? তখন এখানে পার্থক্য তৈরি করে দিতে পারেন এমন একজন ডিজাইনার লাগবে—যিনি শুধু ব্র্যান্ড নয়, ব্যবসার দর্শন, নীতিমালা ও বাজারে আত্মপ্রকাশের কৌশল ঠিক করবেন।
নতুন কর্মসংস্থান বনাম সৃজনশীলতার ভবিষ্যৎ
ভবিষ্যতের এআই হয়তো লেখার কাজ নিয়ে নেবে, কিন্তু মানুষ তখন চিন্তাভাবনার কাজ করবে, বেছে নেবে, গাইড করবে। এথান মোল্লিক যেমন বলেন, “আমি আগে নিজের মতো করে লেখি, না হলে এআই আমার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে।”
পিক্সার-এর উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। হাতে আঁকার যুগে একেকটি ফ্রেমের পেছনে অনেক সময় ব্যয় হতো। কিন্তু প্রযুক্তি এসে সেই কাজ সহজ করে দিয়েছে, গল্প বলার দিকে সময় ও মনোযোগ দিতে পেরেছেন শিল্পীরা।
স্ট্যানফোর্ডের ব্রিনজলফসন বলেন, “আমরা প্রত্যেকে হবো নিজের ছোট এআই সেনাবাহিনীর সিইও।” তার মানে, ভবিষ্যতের অর্থনীতি হবে অনেকটা এমন যেখানে সৃজনশীলতা, উদ্যোগ, রুচি ও জবাবদিহিতা হয়ে দাঁড়াবে সবচেয়ে বড় সম্পদ।
এআই আমাদের জন্য কাজ করবে। কিন্তু সেই কাজকে অর্থপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত করতে হবে আমাদের—মানুষকে। তাই, আমরা যদি নিজের রুচি ঠিক রাখতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতও সুন্দর হতে পারে। এক কথায়, আমরাই হবো এআইয়ের ডিজাইনার।
তথ্যসূত্র: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস
আপনার যদি এ লেখাটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে উইজ বাল্ব বুকমার্ক করে রাখুন। এরকম অভিনব ও নিত্যনতুন লেখা প্রায়ই পাবেন। আপাতত কষ্ট করে একটু ঢুঁ দিয়ে যেতে হবে সাইটে। চেষ্টা করছি নিউজলেটার অপশনও নিয়ে আসতে। সেটা চলে এলে সরাসরি আপনার মেইলেই চলে যাবে নতুন লেখা।